|
কাউন্সিলে চাই শিক্ষা ও নৈতিক নেতৃত্ব, আনুগত্য নয়
রাফায়েল আহমেদ শামীম:
|
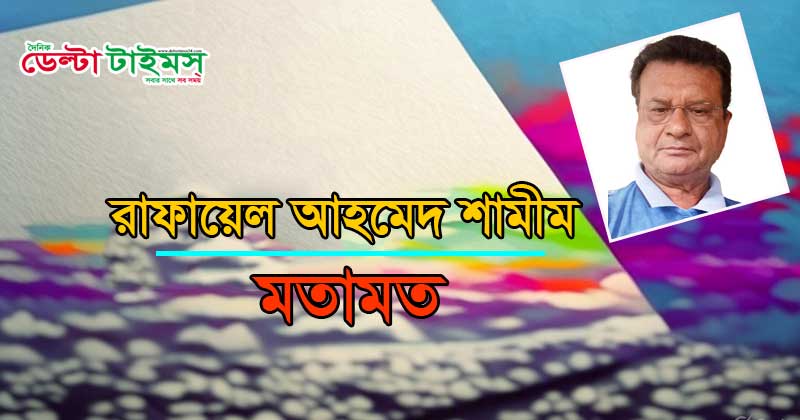 কাউন্সিলে চাই শিক্ষা ও নৈতিক নেতৃত্ব, আনুগত্য নয় বাংলাদেশের জনগণ চিরকালই রাজনৈতিকভাবে সচেতন। তারা জানে কে তাদের স্বার্থে কথা বলে, কে কেবল দলের নির্দেশে চলে। শিক্ষিত নেতার প্রতি তাদের আকর্ষণ স্বাভাবিক, কারণ শিক্ষিত মানুষ সাধারণত নীতি, যুক্তি, বিশ্লেষণ ও দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে কাজ করেন। তারা সমাজকে উন্নয়নের পথে নিতে চান পরিকল্পিতভাবে। তারা জানেন নীতি কেমন হতে পারে, অর্থনীতি কীভাবে কাজ করে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশের মতো বিষয়গুলোতে কীভাবে কার্যকর পরিবর্তন আনা যায়। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি, দলগুলো প্রার্থী মনোনয়ন বা কাউন্সিলে পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে এই যোগ্যতাগুলোকে উপেক্ষা করে। তাদের কাছে প্রাধান্য পায় এমন ব্যক্তিরা যারা দীর্ঘদিন ধরে দলের পতাকা হাতে রাস্তায় ছিলেন, নেতা আসলে যাদের দিয়ে মিছিল করানো যায়, প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করা যায়, কিংবা প্রয়োজনে সংঘর্ষে নামানো যায়। দলীয় রাজনীতিতে “কর্মকাণ্ড” নামের যে মাপকাঠি তৈরি হয়েছে, তা আসলে আনুগত্যের আরেক নাম। কে কতটা কেন্দ্রীয় নেতার প্রতি বিশ্বস্ত, কে কতটা “দলের কথা শুনে” কাজ করে, কে প্রতিবাদ না করে নীরবে দায়িত্ব পালন করে- এসবই এখন যোগ্যতার মানদণ্ড হয়ে গেছে। অথচ জনগণ চায় এমন নেতা, যিনি চিন্তা করেন, ভুল হলে বলেন, “না, এভাবে হবে না।” এই চিন্তাশীল মনোভাবই রাজনীতিকে মানবিক করে তোলে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে রাজনীতির বর্তমান কাঠামোতে “চিন্তাশীলতা” নয়, “চিন্তা ছাড়াই আনুগত্য” পুরস্কৃত হয়। শিক্ষিত নেতারা সাধারণত প্রশ্ন করেন, বিশ্লেষণ করেন, পরামর্শ দেন, এবং প্রয়োজনে মতবিরোধ প্রকাশ করেন। অথচ অনেক দলেই এই মতবিরোধকে অপরাধ হিসেবে দেখা হয়। একবার ভিন্নমত দিলে বলা হয় তিনি “বিরোধী শিবিরে” চলে গেছেন। ফলে শিক্ষিত, যুক্তিবাদী, স্বাধীনচেতা মানুষ ধীরে ধীরে রাজনীতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। তারা মনে করেন, দলীয় রাজনীতিতে তাদের চিন্তার কোনো জায়গা নেই। অন্যদিকে যারা প্রশ্ন না করে কেবল নির্দেশ মানে, তাদেরই পুরস্কৃত করা হয় কাউন্সিল বা পদবণ্টনে। এতে দলীয় কাঠামো আরও দুর্বল হয়, কারণ সমালোচনাহীন রাজনীতি মানে উন্নয়নহীন রাজনীতি। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, দলীয় কাঠামোর ভেতরে গণতন্ত্রের অভাব। দলীয় কাউন্সিল নামের আয়োজন অনেক সময়ই কেবল আনুষ্ঠানিকতা। কারা পদ পাবেন, কারা বাদ যাবেন, তা আগেই নির্ধারিত থাকে। কেন্দ্রীয় কমান্ড থেকে নির্দেশ আসে, “এই নামগুলো রাখা হবে, বাকিদের বাদ দাও।” তৃণমূলের নেতাকর্মীরা সেখানে অংশ নেন মাত্র একটি নামমাত্র ভোট বা করতালির ভূমিকায়। ফলে জনগণের মতামত, স্থানীয় পর্যায়ের গ্রহণযোগ্যতা, কিংবা ব্যক্তির সামাজিক ভাবমূর্তি- সবই উপেক্ষিত থাকে। দলীয় কাউন্সিলের আসল উদ্দেশ্য যেখানে হওয়া উচিত গণতান্ত্রিক নির্বাচন, সেখানে এটি হয়ে দাঁড়ায় “মনোনয়নের বৈধতা প্রদানের” উৎসব। দলগুলো কেন প্রার্থী নির্বাচনের আগে স্থানীয় মানুষের মতামত যাচাই করে না-এই প্রশ্নেরও বাস্তব কারণ আছে। প্রথমত, আমাদের রাজনীতিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ক্ষমতা অস্বাভাবিকভাবে বেশি। তৃণমূলের মতামতকে প্রায় কখনোই গুরুত্ব দেওয়া হয় না। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় কেন্দ্রীয় নেতারা স্থানীয় বাস্তবতা সম্পর্কে জানেন না, আর জানলেও স্থানীয়ভাবে যাদের ওপর নির্ভর করেন তারা দলীয় গোষ্ঠীর অংশ। তারা নিজেদের সুবিধামতো প্রতিবেদন দেন- “এই লোকটা ভালো কাজ করে”, “ওটা প্রতিপক্ষের লোক”-এমন অভিযোগে একজন সৎ ও জনপ্রিয় মানুষও বাদ পড়ে যান। তৃতীয়ত, আমাদের রাজনীতিতে গবেষণা বা জরিপ সংস্কৃতি নেই। উন্নত দেশগুলোয় দলগুলো মনোনয়নের আগে জনমত জরিপ করে, স্থানীয় জনগণের প্রতিক্রিয়া নেয়। কিন্তু বাংলাদেশে এসব প্রায় অনুপস্থিত। এখানে প্রার্থী নির্ধারণ হয় ক্ষমতার কেন্দ্রের ইচ্ছায়, মাঠের তথ্যের ভিত্তিতে নয়। এছাড়া অর্থ ও প্রভাবের রাজনীতি এখন নেতৃত্বের নির্ধারক হয়ে উঠেছে। যার হাতে অর্থ, প্রভাব বা “বলশক্তি” আছে, দল মনে করে সে-ই নির্বাচনে জিততে পারবে, কর্মীদের ধরে রাখতে পারবে, এলাকায় আধিপত্য বজায় রাখতে পারবে। ফলে নীতিনিষ্ঠ কিন্তু সাধারণ বা দরিদ্র শিক্ষিত ব্যক্তি দলীয় পদে জায়গা পান না। তাঁর জ্ঞানের মূল্য থাকে না, কারণ দল এখন জ্ঞান নয়, অর্থ ও প্রভাবের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে। এই বাস্তবতা একদিকে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে, অন্যদিকে তরুণ প্রজন্মকে রাজনীতি থেকে বিমুখ করে তুলছে। এই প্রক্রিয়ার ফলে জনতা ও দলের মধ্যে এক গভীর মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়। জনগণ বুঝে যায়, তাদের মতামতের কোনো মূল্য নেই। দলের মনোনীত নেতা এলাকার মানুষদের ভালোভাবে চেনে না, আবার জনগণও তাকে চায় না। ফলে নির্বাচনের সময় দেখা যায়, জনগণ ভোট দিতে অনীহা প্রকাশ করে, বা বিকল্প হিসেবে স্বাধীন প্রার্থীকে সমর্থন করে। এতে দলীয় রাজনীতির ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে। রাজনীতির এই বাস্তবতা কেবল নেতৃত্বের সংকটই তৈরি করছে না, বরং জাতীয় উন্নয়নেও প্রভাব ফেলছে। শিক্ষিত, দক্ষ ও দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ রাজনীতি থেকে সরে যাওয়ায় নীতি-নির্ধারণের টেবিলে স্থান পাচ্ছে অভিজ্ঞতার বদলে আনুগত্য। এর ফলে দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা পররাষ্ট্রনীতিতেও ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। কারণ যিনি চিন্তা করতে জানেন না, যুক্তি দিতে পারেন না, সমালোচনা সহ্য করতে পারেন না-তিনি কখনোই জাতিকে এগিয়ে নিতে পারবেন না। এখন প্রশ্ন হলো, এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার পথ কোথায়? প্রথমত, দলীয় কাউন্সিলগুলোকে প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক করতে হবে। কাউন্সিল মানে হতে হবে প্রতিযোগিতা, তৃণমূলের ভোট, স্বচ্ছ প্রক্রিয়া। কে প্রার্থী হবেন, তা নির্ধারণ করবে কাউন্সিলের সদস্যরা, কেন্দ্রীয় নির্দেশ নয়। দ্বিতীয়ত, দলীয় মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় গবেষণা ও জরিপের সংস্কৃতি চালু করতে হবে। স্থানীয় জনগণের মতামত যাচাই ছাড়া কোনো প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া উচিত নয়। তৃতীয়ত, শিক্ষিত তরুণদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণে উৎসাহ দিতে হবে। রাজনীতিকে কেবল “ক্ষমতার খেলা” নয়, বরং “সেবার ক্ষেত্র” হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। চতুর্থত, দলের অভ্যন্তরে মতবিরোধ ও ভিন্নমতকে জায়গা দিতে হবে। শিক্ষিত মানুষ প্রশ্ন করবে- এটাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। কিন্তু এখনকার রাজনীতিতে প্রশ্ন করা মানেই “বিরোধিতা।” এই মানসিকতা বদলাতে হবে। দলগুলোকে বুঝতে হবে, যে নেতা ভিন্নমত দেয়, তিনিই আসলে দলকে চিন্তা করতে বাধ্য করেন, ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনেন। শেষ পর্যন্ত কথা একটাই- জনগণ আজো রাজনীতিতে আলোর মানুষ খোঁজে। তারা এখনো বিশ্বাস করে, শিক্ষিত ও নীতিনিষ্ঠ নেতৃত্বই দেশকে সঠিক পথে নিতে পারে। কিন্তু দলগুলো যদি কেবল পথের, শক্তির, আনুগত্যের রাজনীতিতেই আটকে থাকে, তাহলে জনতা আর দল কখনোই একসাথে হাঁটবে না। যে দিন দলগুলো বুঝবে, নেতৃত্ব মানে শুধু লাঠি বা মিছিল নয়, বরং চিন্তা, পরিকল্পনা, চরিত্র ও জনআস্থা সেই দিনই সত্যিকারের দলীয় কাউন্সিল জনগণের কাউন্সিল হবে। তখন হয়তো জনতার মনের সেই প্রশ্ন “দল কেন শিক্ষিত নেতা চায় না?” তার জবাব খুঁজে পাবে দেশের রাজনীতি নিজেই। লেখক : অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কলাম লেখক, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা। ডেল্টা টাইমস/রাফায়েল আহমেদ শামীম/সিআর/এমই |
| « পূর্ববর্তী সংবাদ | পরবর্তী সংবাদ » |